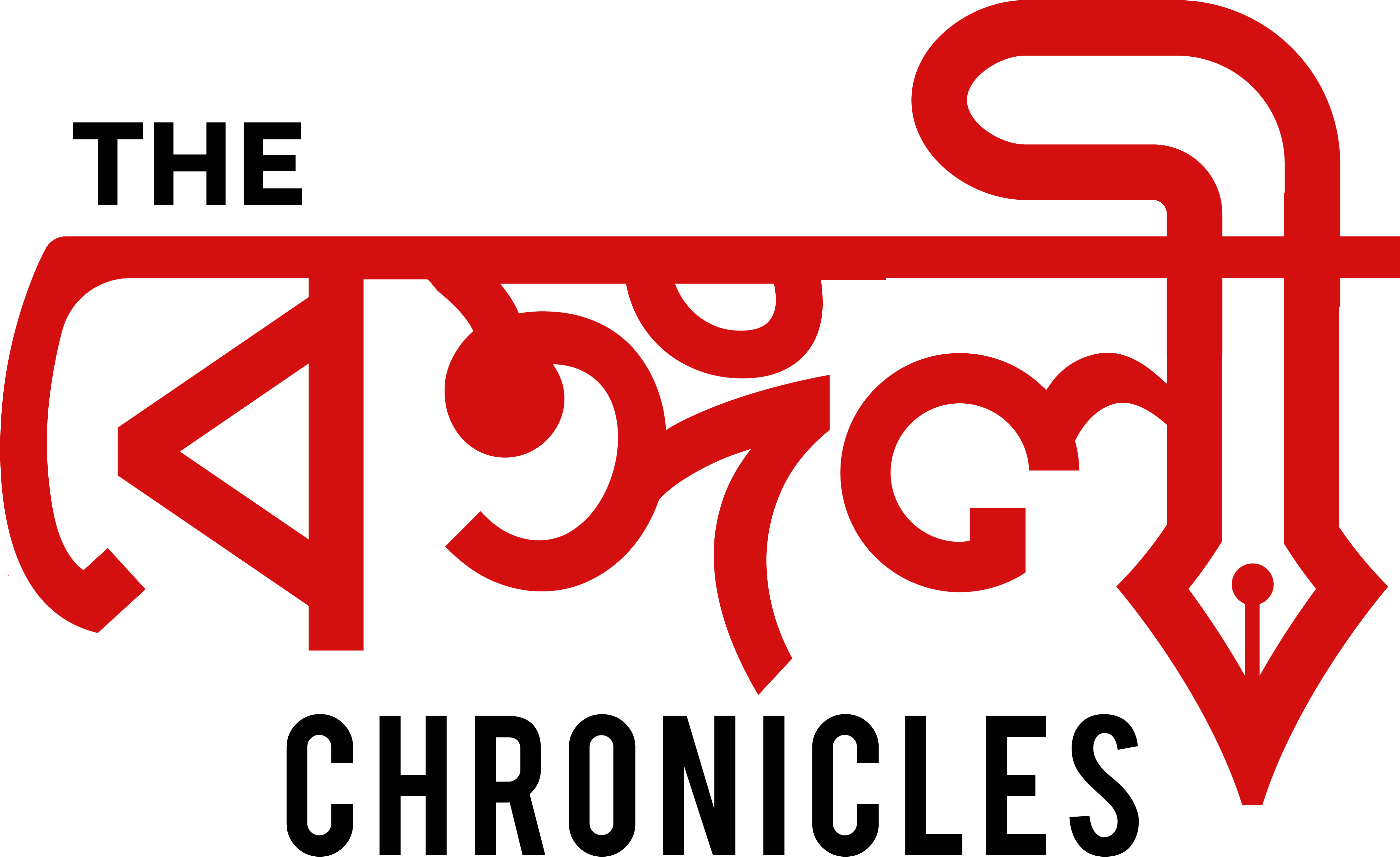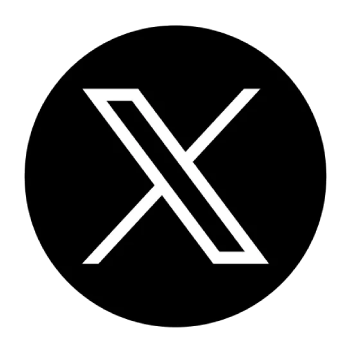কেন বন্ধ হতে বসেছিল Visva-Bharati? গান্ধীজির সাহায্যে কিভাবে সঙ্কট দূর করেছিলেন কবিগুরু?
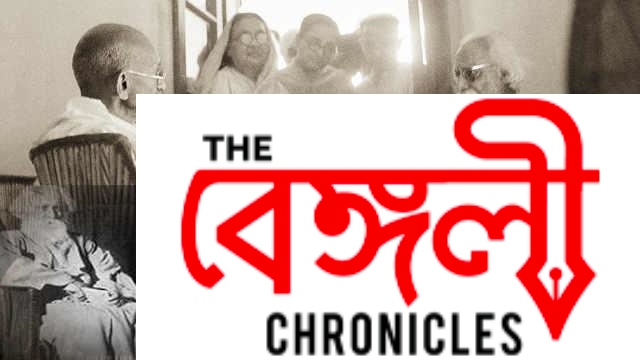
চলন্ত রেলগাড়িতে বসে বিশ্বকবির দেওয়া খামটি খুললেন মহাত্মা। দেখলেন ভিতরে এক চিঠি— “শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আমি আপনাকে সাগ্রহে আবেদন জানাচ্ছি, এই প্রতিষ্ঠানটিকে আপনি নিজ রক্ষনাধীনে গ্রহণ করুন, আর আপনি যদি একে জাতীয় সম্পদ বলে বিবেচনা করেন তবে একে স্থায়িত্বের আশ্বাস দিন। বিশ্বভারতী আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বহনকারী এক জাহাজের মত।”
কবির চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন মহাত্মা

বিলম্ব না করে ট্রেনেই কবির চিঠির উত্তর লিখেছিলেন মহাত্মা— ‘প্রিয় গুরুদেব, ফেরার সময় আমার হাতে আপনি যে মর্মস্পর্শী চিঠিখানা দিলেন, তা সরাসরি আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। বিশ্বভারতী অবশ্যই একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। নিঃসন্দেহে ইহা আন্তর্জাতিকও বটে। আপনি আমার উপর নির্ভর করতে পারেন। শান্তিনিকেতনকে আমি সর্বদা আমার দ্বিতীয় আবাস বলে গণ্য করে এসেছি; এর চিরস্থায়িত্বের জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো। আর দিনের বেলা এক ঘণ্টা করে ঘুমাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আপনি, আশা রাখি তা অতি অবশ্যই পালন করবেন।’
১৯৩৩ সালে Visva-Bharati-তে তীব্র অর্থসংকট দেখা যায়

গান্ধীর সঙ্গে রবিঠাকুর এবং বিশ্বভারতীর যোগ এই প্রথম ছিল না। ১৯৩৩ সালে বিশ্বভারতীতে তীব্র অর্থসংকট দেখা যায়( visva- Bharati )। এমন অবস্থা হয় যে, রবিঠাকুর আশ্রম বন্ধ হতে পারেও বলে ভেবে নিয়েছিলেন। কিন্তু হাল না ছেড়ে বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করতে লাগলেন। তাতে বিশেষ লাভ কিছু হল না। তখন এক দিন অ্যান্ড্রুজ তাঁকে গান্ধীজির কাছে বিষয়টি তুলে ধরার কথা বললেন। কবি প্রথমে ইতস্তত করছিলেন ঠিকই কিন্তু পরে এক প্রকার নিরুপায় হয়েই সব কিছু জানিয়ে গান্ধীজিকে চিঠি লিখলেন।
গান্ধীজি টাকা সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন

অবশেষে গান্ধীজির হাতে যখন চিঠিখানা পড়ল, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আর সময় নষ্ট না করে গান্ধীজি রবিঠাকুরকে জানালেন যে, তিনি টাকা সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তাঁর উপর কবি যেন ভরসা রাখেন। এই বয়সে এসে যে বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভিক্ষা অভিযানে বেরোতে হবে, তা তিনি ভাবতেও পারেন না। যে করেই হোক প্রয়োজনীয় অর্থ তিনি কবির হাতে তুলে দেবেনই।
‘চিত্রাঙ্গদা’ পরিবেশিত হল

কিন্তু শয্যাশায়ী অসুখ ও দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে গান্ধী বিশ্বভারতীর জন্য কিছু করে ওঠার আর অবকাশ পেলেন না। এদিকে রবীন্দ্রনাথও বিচলিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর অর্থের ভীষণই প্রয়োজন। আশ্রমকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অনন্যোপায় কবি আবার বের হলেন টাকার খোঁজে (মার্চ, ১৯৩৬)। কলকাতা, পটনা, এলাহবাদ, দিল্লি হয়ে গেলেন লাহোর পর্যন্ত। সর্বত্র ‘চিত্রাঙ্গদা’ পরিবেশিত হল। লাহোরে পরপর দু’দিন। প্রভূত প্রশংসাও পেলেন। তারপর এলেন দিল্লি। গান্ধীজিও সেই সময়ে দিল্লিতে। ওদিনই সন্ধ্যায় কস্তুরীবাঈকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করলেন কবির সঙ্গে। এরপর ২৬ ও ২৭ মার্চ পরপর দু’দিন দিল্লির রিগাল থিয়েটারে অভিনীত হল চিত্রাঙ্গদা’। ২৭ মার্চ গান্ধীজি ষাট হাজার টাকার একটা চেক পাঠালেন। সঙ্গে ছোট্ট একটি চিঠিতে অবশিষ্ট অনুষ্ঠানসূচি বাতিলের অনুরোধ করলেন— ‘‘এখন আপনি অবশিষ্ট অনুষ্ঠানসূচি বাতিল করে দিয়ে জনসাধারণের মনের উদ্বেগ দূর করুন।’’২৯ মার্চ মীরাঠে ‘চিত্রাঙ্গদা’ অভিনীত হওয়ার কথা। কথা রাখলেন কবি। মীরাঠ থেকে ফিরে পরদিনই (৩০শে মার্চ, ১৯৩৬) এক প্রেস বিবৃতিতে অজ্ঞাতনামা ওই বন্ধুদের দানের কথা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন। তারপর ৩১ মার্চ সদলবলে ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে। আজ সারাবিশ্বে গান্ধীজয়ন্তি পালন হচ্ছে। গান্ধী কিন্তু নেই, আর রবীন্দ্রনাথও নেই। কেবল পরে আছে তাদের আদর্শ, তাদের দৃষ্টি। বিগত কিছু বছর ধরে বিশ্বভারতী নিয়ে যেসমস্ত বিষয় জনসমক্ষে উঠে আসছে, তা দেখলে এই দুই মহাত্মা সত্যিই কী আজকের ভারতবর্ষের উপর আস্থা পেতেন?