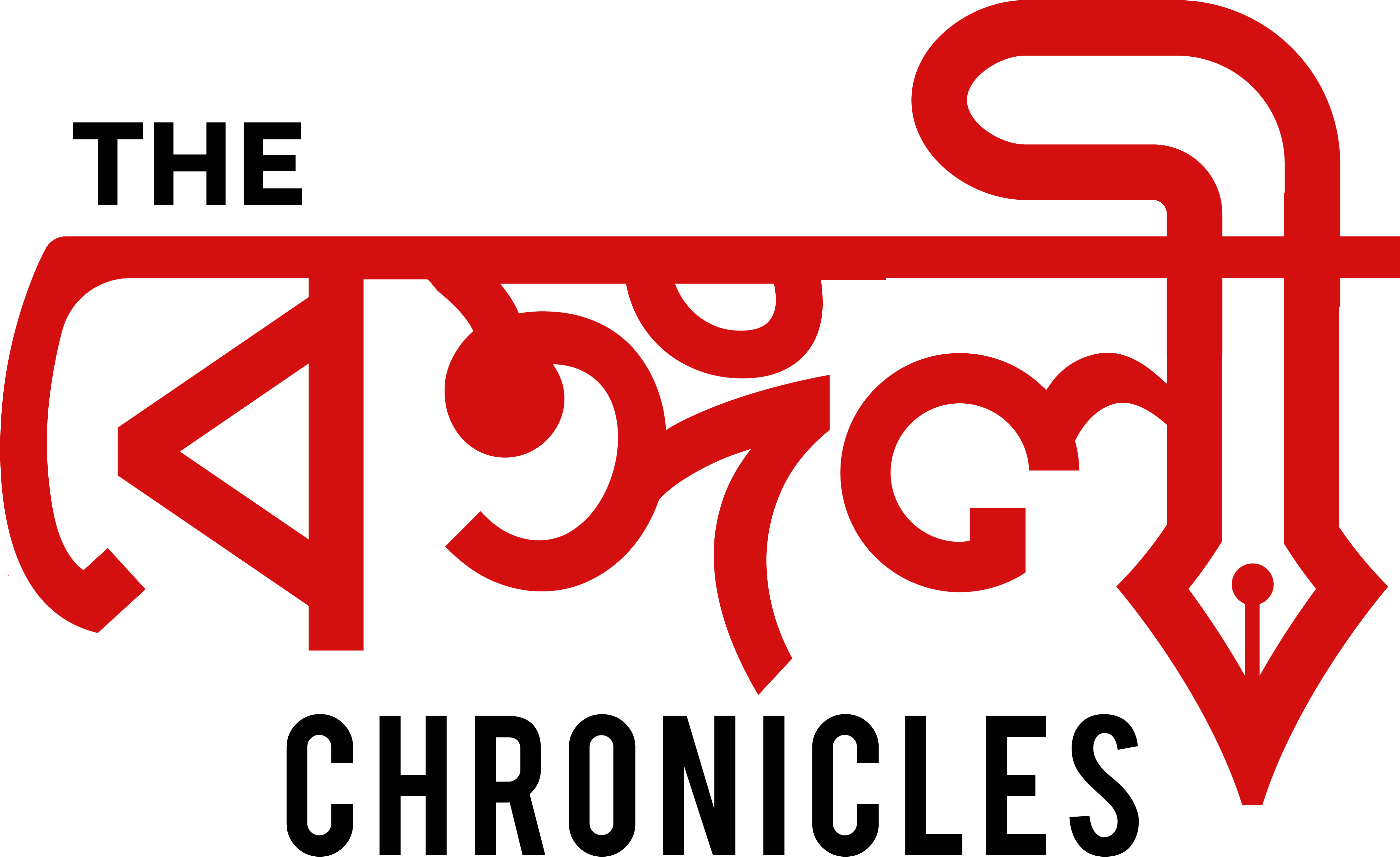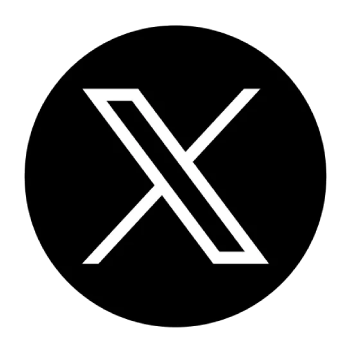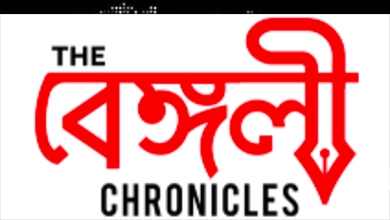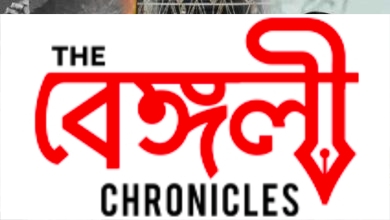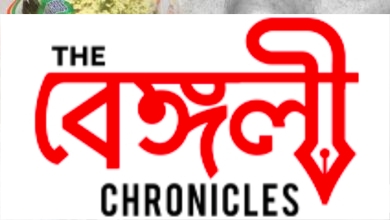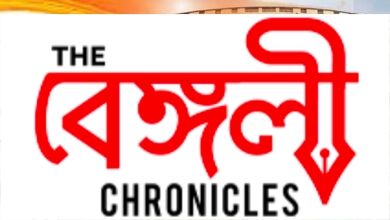Satyajit Roy – হারানো মানিক, সত্যজিৎ-র চোখেই ফিরে দেখা বাঙালীর স্বর্ণযুগের চলচ্চিত্রের চালচিত্র
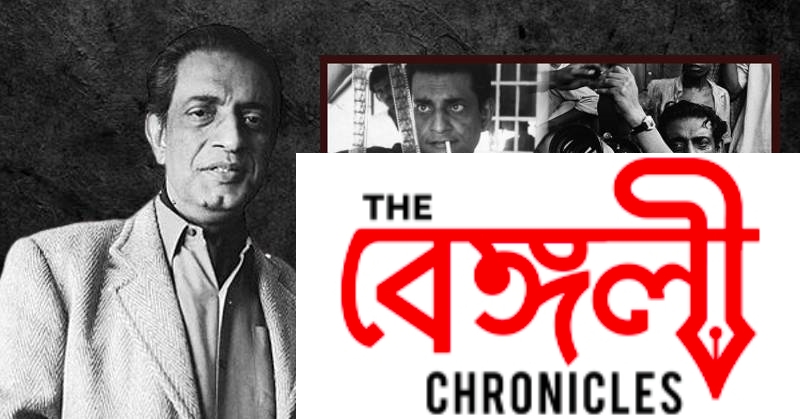
মনে পড়ে সেই বিকালটা, ঘড়ির কাঁটায় বাজে সাড়ে পাঁচটা। পথ চলতি পথিকের মতোই কানে এল একটা সংবাদ… না আদতেই তা দুসংবাদ(Sad News) । ভারত নাকি খোয়ালো তার অমূল্য রত্নকে, অর্থাৎ বলা যেতেই পারে ভারত ‘রত্নহীন’। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের মৃত্যু বিশেষত, বাঙালির মৃত্যু (death)। এপ্রিলের সেই গুমোট গরমের মধ্যে চারপাশ যেন বিষণ্ণ। মাথার মধ্যে নাকি মনের মধ্যে তা বুঝিয়ে বলা কঠিন একটি বিষয় বারংবার নাড়াচাড়া দিয়ে উঠে বলতে লাগলো “নেই সত্যজিৎ” (satyajit roy)। একটি ইংরেজি দৈনিক (English Daily) পরের দিন তাঁদের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে ছিল দ্যা এন্ড অব আ ফেজ (The End of a Phase)”।
সত্যিই তো! একটা পর্যায়ের সমাপ্তিই বটে। বাঙালি তথা ভারতের চলচিত্র বা বলা যেতেই পারে বিশ্বের চলচিত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকবেন এই ব্যাক্তি। কারণ, তিনি যে বিশ্বজিতেষু। চলচিত্রে (film) তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাঙালির কাছে। ঠিক সেই কারণেই হয়তো তাঁর চলে যাওয়াতে এতোটা মূহ্যমান হয়ে পড়েছিল বাঙালি। তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু, বাঙালির প্রতি কৃতিত্ব কখনোই বাঁধা যাবে না কয়েকটা শব্দ, অনুচ্ছেদ, কিংবা কতগুলি পাতার মধ্যে।

বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে জন্ম তাঁর। ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠাটা খানিকটা সাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতির চর্চার মধ্যে দিয়ে। প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করে তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক সময়ে অর্থনীতিকেই বেছে নেওয়া নিজের স্নাতকের পড়াশোনার জন্য। রবি ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধায় শান্তিনিকেতনে চলে আসা এবং তারপর বিশ্বভারতী থেকে পড়াশোনা। প্রাচ্য শিল্পের সঙ্গে পরিচিতি এবং তারপর থেকেই হয়তো তাঁর মনের কোণে শিল্পের বীজ রোপণ হয়ে যাওয়া।
নিজের গোটা জীবনে একাধিক চলচিত্র ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। কর্মজীবনের শুরুতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পথের পাঁচালি” থেকে প্রভাবিত হয়ে সেটিকে চলচিত্রের রূপ দানের সিধান্ত গ্রহণ করেন। এরপরই নিজের জমানো কিছু টাকা থেকে প্রাথমিক দৃশ্যগ্রহণের কাজ শুরু করেন। ভেবেছিলেন হয়তো প্রাথমিক দৃশ্যগুলি দেখার পর কেউ তাঁর ছবিতে অর্থলগ্নি করবে। কিন্তু সব ভাবনাই বৃথা, পেলেন না কোনো অর্থ বিনিয়োগকারীকে। “হাল ছেড়ো না বন্ধু”- এই কথাটি মাথায় নিয়েই নিজের ছোট পুঁজি থেকে ধীরে ধীরে অর্থ বিনিয়োগ শুরু করলেন। অবশেষে, ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ছবি নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন এবং সেই বছর ছবিটি মুক্তি পায়। মুক্তির সাথে সাথেই প্রশংসা ও পুরস্কারে ঘিরে ওঠে তাঁর জীবন।

এরপরই একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর নিজস্ব চলচ্চিত্র। দেবী, অপরাজিত, চারুলতা ইত্যাদি। তাঁর চলচিত্রে প্রতিটি ক্ষুদ্র জিনিসও প্রদর্শিত হত অভাবনীয় রূপে। আবহ সঙ্গীত থেকে চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত চিত্রকলাই ছিল তার গল্পের মূল প্রাণ। তাঁর চলচিত্রগুলিতে নারীদের অবস্থান নিয়ে বেশ প্রশংসা পেয়েছেন তিনি। যেমন উদাহরণ দিতে গেলে বলা যায়, ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’-র জয়া বা কাবেরী বসুর মেমোরি গেমের দৃশ্য। তিনি যখন কানের কাছে হাতের উপর ভর করে মাদুরের উপর আধশোওয়া ভঙ্গিতে আলগা হলেন তখন সেই সাদা ঢাকাইয়ের কালো পাড়ের নকশা তার শরীরে ঢেউ খেলিয়ে দর্শকের মনে জমাট হয়ে গিয়েছিল।
সাহিত্যেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁর লেখা ফেলুদা সিরিজ এখনও জনপ্রিয় ছোট থেকে বুড়োদের মধ্যে। এই সমগ্রের জনপ্রিয়তার জেরে একাধিক সিনেমাও তৈরি করেছিলেন তিনি। বাঙালির প্রতি তাঁর অবদান কখনো শোধ করার নয় এবং তা সম্ভবও নয়। সেই কারণে দিন শেষে এটা বলাই যেতে পারে, শতবর্ষের দরজায় এসে উনি, সত্যজিৎ, বিশ্বজিৎ, জিনিয়াসেরও জিনিয়াস। “যার অবদান ভুলিবার নহে”।